

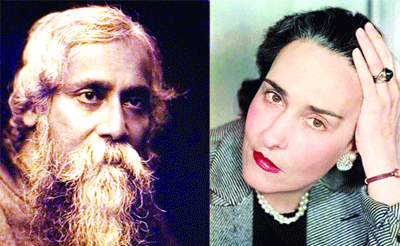
(ভারতের তামিলনাড়ুতে জন্ম রঙ্গরাজ বিশ্বনাথান একজন লেখক, প্রবন্ধকার ও নান্দনিক বাগ্মিতার অধিকারী। তিনি আর. বিশ্বনাথান নামে পরিচিত। দক্ষিণ আমেরিকার শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর তাঁর প্রবল আগ্রহ আছে এবং উক্ত বিষয়ের উপর বিশেষ দখলদারিত্ব অর্জন করেছেন। উক্ত অঞ্চলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি ব্লগে ও সংবাদপত্রে লেখালেখি করেন এবং বিভিন্ন পরিমণ্ডলে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি দক্ষিণ আমেরিকার এসব অঞ্চলে বারো বছর সফল কূটনৈতিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ ভাষায়ও দখল রয়েছে। তাঁর লেখা দু’টি ইংরেজি প্রবন্ধ থেকে লেখাটি ভাবানুবাদ করা হয়েছে।)
এক.
রবি ঠাকুর ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সম্পর্ক আজও গোলকধাঁধার মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। রবি ঠাকুরের ‘পূরবী‘ কাব্যের অনুপ্রেরণার যোগানদাত্রী হিসেবে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো মুখ্য ভূমিকা পালন করেন; ফলে রবি ঠাকুর পূরবী কাব্যটি ওকাম্পোর চরণে বলিদান করেন। ‘ল্যাতিন আমেরিকার ভদ্রমহিলাদের অনুরাগ, আবেগ ও ভালোলাগা প্রকাশের একটা বিশেষায়িত পথ আছে’- রবি ঠাকুরের চিন্তার মনোজগত এমন চিন্তা দ্বারা আলোড়িত হত। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ছিলেন রবি ঠাকুরের আর্জেন্টাইন ভক্ত ও অনুরাগী যিনি বুয়েন আয়ার্স থেকে ভারতে একটি আর্মচেয়ার বিশেষ উপডৌকন হিসেবে পাঠিয়েছেন। কিন্তু সেখানে একটা সমস্যার উদ্ভব হয়। চেয়ারটি এতটাই বড়ো ছিল জাহাজে ঠাকুর মহাশয়ের জন্য নির্ধারিত বিশেষ কামরায় ঢুকানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু ওকাম্পোর দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি উক্ত অসাধ্য সাধন থেকে ইস্তফা দিলোনা।ওকাম্পো জাহাজের ক্যাপ্টেনকে কামরার দরজা ভেঙে প্রবেশপথকে প্রশস্ত করে চেয়ারটি ঢুকানো জন্য বললেন। এই সেই ওকাম্পো যিনি দু’টি বিছানাবিশিষ্ট বিশেষ কামরা ঠাকুর মহাশয়ের প্রস্তুত করলেন তাঁর বিশেষ যোগাযোগের মাধ্যমে। এই সুব্যবস্থাই ঠাকুর মহাশয়কে উল্লিখিত মন্তব্য করতে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ১৯২৪ সালে নভেম্বর-ডিসেম্বর এ দু’মাস ওকাম্পো’র অতিথি হিসেবে ঠাকুর মহাশয় বুয়েন আয়ার্সে অবস্থানকালে উক্ত চেয়ারটিতে বসেছিলেন। চেয়ারটি এখনো শান্তিনিকেতনে রক্ষিত রয়েছে। ঠাকুর মহাশয়ের জীবনের শেষ দিনগুলিতে উক্ত চেয়ারটি বসে আরাম করেছেন, এমনকি কবিতাও লিখেছেন ১৯৪১ সালে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। ঠাকুর মহাশয়ের তিরোধানের সংবাদ পাওয়ার পরে ওকাম্পো মহাশয়ের পুত্রের কাছে একটি টেলিগ্রাম করেন। যার টাইটেল ছিল ‘থিংকিং অব হিম’ (pensando en el)। আর্জেনটাইন সিনেমাটি উক্তি শিরোনাম দিয়েই নির্মিত করা হয়েছে।

পাবলো সিজার, আর্জেনটাইন পরিচালক ও প্রযোজক যিনি ওকাম্পো-ঠাকুর মহাশয়ের সরাসরি সাক্ষাতের জীবনঘনিষ্ঠ বাস্তব গল্পটি এ চমৎকার সিনেমাটি তৈরি করেছেন। ঠাকুর মহাশয়কে পেরুর স্বাধীনতার শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়ানোর উদ্দেশ্যে যাত্রাবিরতে ৬ই নভেম্বর বুয়েন আয়ার্সে কিছুক্ষণ অবস্থান করতে হয়েছিল। ওকাম্পো এ খবরটা জানতে পারলেন এবং ঠাকুর মহাশয়কে তার আতিথিয়েতা গ্রহণের উষ্ণ আহ্বান জানালেন। ওকাম্পো তার মূল্যবান অলঙ্কারসামগ্রী বন্ধক রেখে বুয়েন আয়ার্সের উপশহর ‘স্যান ইজিড্রো’তে একটি মনোরম বাংলো ভাড়া নেন এবং সেখানে ঠাকুর মহাশয়কে কিছুদিনের জন্য রাখেন। উক্ত বাংলোর বেলকনি থেকে তিনি সমূদ্রের মতো প্রশস্ত ‘প্লেতা নদী’ এরং বিশাল উদ্যানের সরু সরু গাছ ও মনোমুগ্ধকর ফুলের মনোরম দৃশ্য অবলোকন করতেন। তিনি অসুস্থতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করে ১৯২৫ সালের ৩রা জানুয়ারি বুয়েন আয়ার্স ত্যাগ করেন। আটান্ন দিনের অবস্থানকালে তেষট্টি বছরের ঠাকুর মহাশয় চৌত্রিশ বছরের যুবতী ওকাম্পোর সেবা-যত্নে নবরূপে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেন। সম্পূর্ণ ভক্তি দিয়ে ওকাম্পো ঠাকুর মহাশয়কে সেবা-যত্ন করেছেন এবং মহাশয়ের কল্পনাকে উত্তপ্ত করেছেন। অন্যদিকে ওকাম্পো ভারতীয় এই মহান দার্শনিক-কবির কাছ থেকে আধ্যাত্মিকতার দীক্ষা ও নান্দনিকতার উৎসাহ-উদ্দীপনা পেতে সক্ষম হয়েছেন। ওকাম্পো-ঠাকুর মহাশয়ের আধ্যাত্মিক ও অদৈহিক ভালোবাসা একে অপরের সাথে বিনিময় হলো এবং তাঁদের মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক সূচিত হল।
কে এই ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো? অনেক ভারতীয়ই তাঁর সম্পর্কে জানে না। ওকাম্পো একজন লেখক এবং শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। আর্জেনটাইন সাহিত্যে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি দেশীয় গণ্ডির খোলস থেকে মুক্ত হয়ে ল্যাতিন আমেরিকা, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভুবনের সাথে সেতুবন্ধের রচনা করেছেন। প্রথম মহিলা হিসেবে সর্বপ্রথম ১৯৭৭ সালে আর্জেনটাইন একাডেমি অব লেটারস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। এটাই ছিল এই ‘জ্ঞানের রাণীর’ বিশেষ তৃপ্তির জায়গা যিনি তাঁর জীবনের যৌবনকালে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অস্ত্রাঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে লেখালেখির প্রতি উৎসাহ হারিয়েছেন, নির্মম অবহেলার শিকার হয়েছেন এবং বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। ওকাম্পো সাহিত্য ম্যাগাজিন ‘সার’ প্রতিষ্ঠা করেন, অর্থায়ন করেন, প্রকাশনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত ম্যাগাজিনটিতে দেশি এবং আন্তর্জাতিক লেখক ও কবিদের কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও সামাজিক ইস্যু স্থান পেত। ওকাম্পো একজন চরম নারীবাদী যিনি তাঁর সময়ের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। তিনি তার অসুখী বিয়ের পাঠ দ্রুত চুকিয়ে জীবনের বাকি সময়টুকু স্বাধীনভাবে যাপন করেন। তিনি পৃথিবীটা ভ্রমণ করেন এবং ইউরোপের বিশেষকরে ফ্রান্সের শিল্প-সাহিত্য ও সামাজিক পরিমণ্ডলে ঘুরে বেড়ান।
ওকাম্পো ১৯১৪ সালে গীতাঞ্জলি পড়ে এই মন্তব্যটি করেন, ‘কাব্যটি আমার চব্বিশ বছরের যন্ত্রণাময় হৃদয়ে স্বর্গীয় শিশিরের মতো পতিত হয়েছে।’ তিনি ঠাকুর মহাশয়ের এ কাব্যকে ‘জাদুকরি রহস্যপূর্ণ ভাবনা’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজের মধ্যে ঠাকুর মহাশয়ের প্রিয় ঈশ্বরের শক্তিশালী অনুরণন অনুভব করলেন যা সুখ ও শান্তির জ্যোতি ছড়ায়, এমন প্রতিশোধপরায়ন ঈশ্বর নয় যা শৈশবে তাঁর জীবনে ঘাপটি চেপে বসেছিল। তিনি খুবই উচ্ছ্বসিত ছিলেন যখন ১৯২৪ সালে ৬ই নভেম্বর ঠাকুর মহাশয় বুয়েন আয়ার্সে আসলেন। তাঁর কথায় এটা তাঁর জীবন সবচেয়ে বড়ো ঘটনাগুলোর একটি। তিনি আর্জেনটাইন দৈনিক ‘লা ন্যাশন’ (La Nacion) ৯ই নভেম্বর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাঠে আনন্দ’। তিনি ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিভা ও নিবিড়তায় ভীতসন্ত্রস্ত হন এবং নিজেকে তাঁর সামনে বাচ্চা শিশুর মতো লাজুক মনে করেন। তিনি ঠাকুর মহাশয়ের কথা সবসময়ই শুনতেন, তাঁর সহজাত প্রবনতা লুকিয়ে রাখতেন এবং কোনকিছুই প্রকাশের সাহস করেননি। পরবর্তীতে ‘প্লেতা নদীর তীরে ঠাকুর’ এবং ‘স্যান ইজিড্রো নদীতে ঠাকুর’ লেখা দু’টিতে তিনি তাঁর স্মৃতিচারণ করেছেন। ওকাম্পো ঠাকুর মহাশয়কে তাঁর সামাজিক ও শৈল্পিক ভুবনের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন এবং আর্জেনটাইন পত্র-পত্রিকায় ঠাকুর মহাশয়কে নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন।
ওকাম্পো ঠাকুর মহাশয়ের পূরবী কাব্য সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন যেখানে তিনি ওকাম্পোকে বিজয়া (Victoria) নামে উল্লেখ করেছেন। পূরবী কাব্যটি ঠাকুর মহাশয় ওকাম্পোকে উৎসর্গ করেছেন। ভারতে ফিরে ঠাকুর মহাশয়-ওকাম্পোর মধ্যে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত চিঠি চালাচালি হয়। ঠাকুর মহাশয় ওকাম্পোকে ‘আমার ভালোবাসা’ নামক উষ্ণ সম্বোধন চিঠির শুরুতে উল্লেখ করতেন। ওকাম্পো ঠাকুর মহাশকে ‘প্রিয় গুরুদেব’ নামে সম্বোধন করতেন এবং ‘তোমার বিজয়া’ নামে নিজের স্বাক্ষর দিতেন। ওকাম্পোর সাথে প্রথম দর্শনে ঠাকুর মহাশয় নিজের মধ্যে উচ্চারিত করেন, ‘আমার মুখের সবকথা যখনই বিলুপ্তি হয়, নতুন সুর আমার হৃদয় হতে আসে আনমনে, হে প্রিয়া তোমার মুখ-দর্শনে’। ওকাম্পোর নিজের মধ্যে যে সুর উঠতো তা হল- ‘আমি যখনই তোমার সন্নিকটে যাই, পরক্ষণে এই ভেবে অসুখী হই, তুমিতো আমার বন্ধনের কি কেউ?’ ঠাকুর মহাশয় লিখেন, ‘সুখের ছোঁয়া, তোমার সান্নিধ্যে আমি আনন্দিত হই; বিরহে জ্বলা, তুমি যখনই অগ্রাহ্য করো আমার শিহরণ।’ ঠাকুর মহাশয় ওকাম্পকে লিখেন, ‘আমার জীবনের বেলা অবেলায়, তুমিই যদি আসতে কোমল স্পর্শতায়। আমরা যদি বাঁধতাম বাঁধন, শব্দে শব্দে খেলতাম দুজন, হাসতে পারতাম মনের মতন।’
ঠাকুর মহাশয় তাঁর কাছে একাকীত্বের ভারি পাথরটি বহনের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন, নারীপ্রেমের আকাঙ্ক্ষার কথা, তার অতৃপ্ততার কথা ও বয়ে চলা জীবনে মানবীর পাশে থাকার কথা প্রকাশ করেছেন-দু’জনের একান্ত আলাপচারিতায় । ওকাম্পোর হৃদয়ে অজানা এক হাহাকার অসীম তীব্রতায় বাঁধভাঙা স্রোতের মতো নেমে আসলো, ‘কেনোগো এত তাড়াতাড়ি চলে গেলে, একাকী ফেলে মোরে।’ ‘ তোমার স্মৃতি আঁকড়ে আমি, তোমায় আমি ভীষণভাবে ভাবি।’ ‘তুমি বিনে আমার দিনগুলি, এক সংখ্যাহীন সংখায় গুনি।’ ‘আমি শঙ্কিত, তুমি জানবে না আমি যে কত তোমায় পূজি।’ ‘মনে রেখো গুরুদেব, এখানে এমন কাউকে ফেলে রেখে গেছ যে তার ভালোবাসার অভিব্যক্তি তোমাতে খুঁজে।’ এমন আবেগঘন বার্তা বিনিময় হতো দু’জনের হৃদস্পন্দনের যোগাযোগে। তাঁদের দু’জনের সাক্ষাৎ মহাদেশীয় যোগাযোগের সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। ঠাকুর মহাশয় তাকে লিখেছেন, ‘আমার হৃদয়ে তোমার অবয়ব ল্যাতিন আমেরিকার আত্মা হিসেবে সারাজীবন বসবাস করবে।’ ওকাম্পো জবাবে বললেন, ‘তুমি সর্বদাই আছ এবং থাকবে আমার হৃদয়ে, ভারতমাতা রূপে।’
চলচ্চিত্রটির দু’টি ভিন্ন ভিন্ন বিকল্প অংশ রয়েছে-সাদাকালোর দৃশ্যে ওকাম্পো-ঠাকুর মহাশয় এবং রঙিন দৃশ্যে আর্জেনটাইন এক শিক্ষকের ঠাকুর মহাশয়ের শিক্ষাপদ্ধতি অনুধাবনে শান্তিনিকেতন পরিদর্শন।ওকাম্পো-ঠাকুর মহাশয়ের দৃশ্যগুলো নিখুঁত ও নান্দনিকভাবে ফুটে উঠেছে, কিন্তু গল্পের অপর অংশটি শক্তিশালী ও চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়নি। ইলিওনারা ওয়েক্সলার, আর্জেনটাইন অভিনেত্রী, যিনি ওকাম্পোর চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন। যিনি বিশ শতকের আবেগ-অনুভূতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে তৎকালীন আর্জেনটাইন নারীর প্রতিকৃতিতে নিজেকে তুলে ধরেছেন।ভিক্টোর ব্যানার্জি রবি ঠাকুরের সংবেদনশিলতায় নিজেকে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন।
দুই.
‘থিংকিং অব হিম’ চলচ্চিত্রটির রিভিউ পাঠের পর রবি ঠাকুর ও আর্জেনটাইন লেখিকা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সম্পর্ক যে কারো মধ্যে কৌতূহলী জানার অনুষঙ্গ তৈরি করতে পারে। আসলেই এই আধ্যাত্মিক সম্পর্কের মধ্যে দৈহিক সান্নিধ্যের কোনো অংশ আছে কিনা।?
আর্জেনটাইন উপলব্ধি ও চিন্তার পরিক্রমায়-এ সম্পর্ক জটিলতার জটলায় আবদ্ধ। আর্জেনটাইন কথ্য অভিধায় যে শব্দটি সচরাচর ব্যবহৃত হয় সেটি হলো ‘জটিল’ (complicado)। কোনো আর্জেনটাইনকে তার দেশ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ঋণ, বিবাহ, প্রেম-ভালবাসা, আবহাওয়া কিংবা বিশ্বপরিস্থিতি নিয়ে কোনোকিছু জিজ্ঞেস করলে, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্ভাষণ ‘চে’ (বন্ধু) উচ্চারণ করে ব্যাপারটা ‘জটিল’ বলে ব্যাখ্যা কিংবা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। যখনই ঠাকুর মহাশয়-ওকাম্পোর সম্পর্কের অনুষঙ্গটি আসে, তখনই এ দ্ব্যর্থক বিশেষণটি সম্পর্কের গতি-প্রকৃতির নিরপেক্ষ অনুসন্ধানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।
‘নায়িকা’ তাঁর সীমারেখা অঙ্কন করলেন; ‘নায়ক’ এ সীমারেখা লঙ্ঘন করেননি। কিন্তু তিনি প্রলুব্ধ হয়েছেন…. চেষ্টা করেছেন- শুধুই স্পর্শ… সীমারেখা লঙ্ঘিত ব্যতীত। ওকাম্পো তাঁর আত্মজীবনীতে একথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন- ‘একদিন দুপুরে আমি তাঁর কক্ষে আসলাম, তিনি তখন লিখতেছিলেন আর আমি টেবিলে রাখা তাঁর লেখার পাতাটির দিকে ঝুঁকেছিলাম। আমার দিকে না তাকিয়েই, মাথা নিচু অবস্থায় রেখে তিনি তাঁর একটি বাহু প্রসারিত করলেন; যেমন কেউ পাঁকা ফলের গাছের ডালে ফল ধরার জন্য হাত প্রসারিত করে এবং তিনি আমার একটি স্তনের উপর হাত রাখলেন। আমার ভিতরে একটা অস্বীকৃতির ঝাঁকুনি দিল যেমন কোনো ঘোড়া তার মালিক আঘাত করলে সেই আঘাত ঘোড়াটি প্রত্যাশা করে না। তাৎক্ষণিক আমার ভেতরের জন্তুটি চিৎকার করে উঠলো। আবার আমার ভেতরের আমিটি (মানুষটি) জন্তুটিকে সতর্ক করল ‘শান্ত হও, হে বোকা’। এটা মূলত আদিম আবেগের ইঙ্গিত। কোনো ধরনের দৈহিক ক্ষুধা নিবারণ ছাড়াই ফলন্ত গাছের ডাল থেকে হাতটি সরে গেল। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর কখনো ঘটেনি। প্রতিদিন তিনি আমার কপালে কিংবা কপোলে চুমো খেতেন এবং আমার বাহুর যেকোনো একটি স্পর্শ করতেন ‘হে শান্ত, কোমল বাহু’।
এতটুকু দৈহিক সান্নিধ্যে ঠাকুর মহাশয় যেতে পেরেছেন। ওকাম্পোর দয়াশীল ও শান্ত কিন্তু দৃঢ় ও শীতল নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ঠাকুর মহাশয়কে এ সীমারেখায় নিয়ে থামিয়ে রেখেছে। ওকাম্পো ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি তাঁর আবেগের ঘনীভূতকে ‘কোমলতার ভালোবাসা’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এমন ভালোবাসা যার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ভিন্ন অন্য কিছু ঢুকতে পারেনি। ঠাকুর মহাশয় অবশ্য তাঁর ভালোবাসা ও নির্ভরতার কথা কাব্যিক ঢংগে কিন্তু সূক্ষ্ম ও ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলেছেন তাঁর গানে, পত্রে কিংবা কবিতায়।
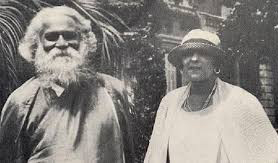
জটিলতার জটিল তত্ত্ব :
ঠাকুর মহাশয়ের ব্যক্তিগত সচিব লিওনার্দো ইলমহার্স্ট (যিনি দক্ষিণ আমেরিকার ভ্রমণের সময় সফরসঙ্গী ছিলেন) ঠাকুর মহাশয়কে অতিক্রম করেছেন ওকাম্পোকে আবিষ্কারের ক্ষেত্রে। গাড়িতে সফরকালে তিনি ওকাম্পোকে চুমো খাওয়ার চেষ্টা করলেন। ওকাম্পো তাঁর গালে কষে থাপ্পর মারলেন এবং সজোরে গাড়ির দরজায় আঘাত করলেন যেন শব্দটি ‘সমস্ত শহরকে কাঁপিয়ে দিল’। পরে ইলমহার্স্ট ওকাম্পোর নিকট ক্ষমা চাইলেন। ওকাম্পো তাঁকে মার্জনা করলেন এবং তিনি পরবর্তীতে এ নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করেননি। ওকাম্পো তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন ইলমহার্স্ট তাঁর দ্বারা বিমোহিত হয়েছেন। তিনিও তাঁর প্রতি কিছুটা আকর্ষণ অনুভব করতেন। এজন্যই তিনি বহুবছর ধরে ইলমহার্স্টের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন এবং ইংল্যান্ডে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেছেন। ঠাকুর মহাশয়কে নিয়ে ওকাম্পোর লেখা বই তিনি ইলমহার্স্টকে উৎসর্গ করেন এই বলে ‘একজন বন্ধু, ঠাকুর মহাশয়ের বন্ধু, ভারতমাতার বন্ধু’।
১৯১২ সালে ওকাম্পো তাঁর অসুখী বৈবাহিক জীবনের গল্প ইলমহার্স্টের কাছে স্বীকার করেছেন। তাঁর স্বামী তাঁকে কীভাবে ‘বিজিত ভূখণ্ডে’র ন্যায় ব্যবহার করতেন- সেকথা বলতেও ভুল করেননি। বিয়ের পাঁচ মাসের পরে তিনি তাঁর গোপন প্রণয়ের নটরাজকে আবিষ্কার করলেন। এই গোপন প্রণয়ের নটরাজ ছিলেন জুলিয়ান মার্টিনেজ নামের তাঁর এক কাজিন। যেহেতু বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি মিলল না এবং তিনি তাঁর পরিবারের কাউকে কষ্ট দিতে চাননি, সেহেতু তিনি স্বামীর সাথে একই ছাদের নিচে আলাদা আলাদা শয়ন কক্ষে বসবাস শুরু করলেন। ১৯২২ সালে স্বামীর বাসা সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে নিজের বাসভবনে আলাদাভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। ঠাকুর মহাশয় কিংবা ইলমহার্স্ট কেউই তাঁর গোপন প্রণয়ের কথা জানতোনা। যদি তাঁরা এ প্রণয়ের কথা জানতো, তবে এমন দুর্ঘটনা নাও ঘটতে পারতো।
ওকাম্পোর অতিশয় ভক্তি ও প্রণাম ঠাকুর মহাশয় ভুলভাবে উপলব্ধি করে আরো বহুকিছুর আকাঙ্ক্ষা করেছেন। ঠাকুর মহাশয়ের সাক্ষাতের সময় ওকাম্পো তাঁর স্বামীর সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেছেন এবং কাজিনের সাথে গোপন প্রণয়ে জড়িয়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন। তাঁর লেখিকা হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষার উপর তাঁর সমাজব্যবস্থা ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিয়ে আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করে দিল। একই সাথে সরাসরি বিরোধিতা করে তিনি তাঁর পরিবারকে কষ্ট দিতে চাননি। তিনি তাঁর পৈত্রিক বৃহৎ বাড়িতে ঠাকুর মহাশয়কে এনে রাখতে চাইলেন কিন্তু তাঁর মা-বাবা এ সিদ্ধান্তে বাঁধা দিলেন। তাঁর এ মনোজাগতিক যন্ত্রণার উত্থান-পতনের সময় তিনি প্রাচ্যের ঠাকুর মহাশয়ের দিকে তীর্থের কাকের মতো তাকিয়েছিলেন। তিনি ভাবনায় ছিলেন যে গুরু মহাশয় তাঁর ভিতরকে আলোকবিচ্ছুরণ দ্বারা আলোকিত করে নতুন পথের সঠিক সন্ধান দিবেন। তাঁর এ ভিতরগত ভাঙা-গড়ার মধ্যে প্রশান্তির ফোয়ারা লাভের প্রত্যাশায় তিনি ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তির অসাধারণ ও বাহ্যিক প্রকাশ ঘটিয়েছেন।
বৃদ্ধ বিপত্নীক কবি ওকাম্পোর অতিশয় ভক্তিকে ভুলভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং দৈহিক সম্পর্কের ইতিবাচক বার্তা হিসেবে নিয়েছেন। তিনি ভেবেছেন, “তিনি দীর্ঘদিনের একাকীত্বের পরে ‘নারীপ্রেমে’র সবুজসংকেত পেয়েছেন, যে প্রেম কোনো পুরুষের ভিতরের হাহাকারকে লাঘব করে যেমন এক বোতল জল মরুভূমিতে সফররত যে কারো বুকের তৃষ্ণা লাঘব করে।” তাঁর ‘শেষ বসন্ত’, কবিতায় তাঁর এ হাহাকারটি তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে, কবিতাটি তিনি ওকাম্পোর আতিথিয়েতায় থেকে ২১ নভেম্বর লিখেছেন।

ওকাম্পো-ইলমহার্স্টের একে অপরের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধ ঠাকুর মহাশয়ের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তিনি সেটা কীভাবে মোকাবেলা করলেন? তিনি ইলমহার্স্টকে এই বলে খোঁচা দিলেন যে তাঁর (ইলমহার্স্ট) ওকাম্পোকে বিয়ে করে শান্তিনিকেতন নিয়ে আসা উচিত। ঠাকুর মহাশয় ভালো করে জানতেন যে ইলমহার্স্ট ‘ড্রোথি’ নামের আমেরিকার এক সম্ভ্রান্ত নারীর সাথে বাগদত্ত এবং শীগ্রই (১৯২৫ সালের এপ্রিলে) তাঁরা বিয়ে করতে যাচ্ছেন। অন্যদিকে ঠাকুর মহাশয় ওকাম্পোকেও বলেছেন যে ইলমহার্স্ট তাঁর প্রেমে পরেছে। মরমি কবির মনে কী দূরভিসন্ধি?
ওকাম্পোকে নিয়ে ঠাকুর মহাশয় ও ইলমহার্টের অনুসন্ধান কোনো ধরনের রিরহগাঁথা তৈরি করেনি। সেক্ষেত্রে ওকাম্পো ছিলো অনেকটাই অগ্রগামী। যেহেতু ওকাম্পো একা, স্বাধীনচেতা, স্বামীহীনা, বৃত্তশীলা ও সুন্দর যুবতী নারী ছিলেন, সেহেতু অনেক পুরুষই তাঁর প্রতি প্রলুব্ধ হতেন। ওরতেগা গেসেট নামের এক স্প্যানিশ কবি, যিনি ওকাম্পোর চেয়ে বয়সে বড়ো ছিলেন, তাঁকে প্রবলভাবে বিপদগামী ও প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছেন। ওকাম্পো কবির এ চারিত্রিক অধপতনকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু কবি হিসেবে তাঁকে ওকাম্পো পছন্দ করতেন এবং তাঁর সঙ্গে সাহিত্য সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে যোগাযোগ রক্ষা চলতেন। পরে ওকাম্পো বয়স্ক ও যুবক অনেক পুরুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। কিন্তু একটা বিষয় খুবই পরিষ্কার। ওকাম্পো কারো স্ত্রী বা প্রেমিকার তকমা লাগিয়ে জীবন চালাতে চাননি।
ওকাম্পো তাঁর নিজের নিয়ন্তা ও পরিচালনের গতি নিজ হাতে রক্ষিত রাখলেন। তার নির্মিত সীমারেখা লঙ্ঘন করে কেউ তাঁর জীবনকে কলুষিত করুক-সেই সুযোগ তিনি কাউকে দেননি। সম্ভবত এই মুখ্য কারণেই ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের নিমন্ত্রণ ওকাম্পো বারবার ফিরিয়ে দিয়েছেন। তিনি নিজেকে এমন সেবিকা হিসেবে কল্পনা করেননি যেমন পশ্চিমা সংস্কৃতির নারী নিবেদিতা ও মিরাবেন স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর সেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন। ওকাম্পো লিখেছেন, ‘আমি তাঁদেরকে ঈর্ষা করি না কারণ আমি জানি আমার ধর্ম আমাকে আমার মতো তৈরি করেছে, তাঁদের ধর্ম তাঁদেরকে তাঁদের মতো তৈরি করেছে, আমার ধর্মের মতো নয়।’
ওকাম্পোর সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের আগে ও পরে অনেক বিদেশী ও ভারতীয় নারী ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন এবং তিনিও অনেক নারীর প্রতি বিমোহিত হয়েছেন। ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৪১ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত, এই সতেরো বছর ঠাকুর মহাশয়ের জীবনে ওকাম্পোই মূল অনুপ্রেরণার উৎস ছিল। পূরবী কাব্য তাঁকে উৎসর্গ করার পাশাপাশি, ঠাকুর মহাশয় আরো অনেক কাব্যে, গল্পে ও চিত্রকর্মে ওকাম্পোকে চিত্রায়িত করেছেন।
ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কন প্রতিভার দ্যুতি প্রকাশে ওকাম্পো একক কৃতিত্বের দাবিদার। ওকাম্পোই বুয়েন আয়ার্সে ঠাকুর মহাশয়ের শিল্পপ্রতিভা অবলোকন করেছেন এবং তাঁকে আঁকতে ব্যাপকভাবে উৎসাহ দেন। ১৯৩০ সালে মে মাসে ওকাম্পো তাঁর নিজ উদ্যোগ, অর্থায়ন ও যোগাযোগে ঠাকুর মহাশয়ের চিত্রকর্মের প্রদর্শনী প্যারিসের ‘গ্যালারি পিজালে’তে ব্যবস্থা করেন। প্যারিসের সংবর্ধনা ও উষ্ণ অভিবাদনে ঠাকুর মহাশয় প্রবল উৎসাহে নতুন নতুন চিত্রকর্ম সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন এবং পরে অনেক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন।
আর্জেনটাইন উপলব্ধির সর্বোচ্চ অনুধাবনমাত্রা থেকে সারসংক্ষেপ করা যায়, ওকাম্পো-ঠাকুর মহাশয়ের সম্পর্ক ‘ট্যাংগো’ নাচের মতো যেখানে নারী-পুরুষের দৈহিক সান্নিধ্য ‘স্ফুলিঙ্গ তৈরি করে কিন্তু একে-অপরকে দৈহিক দহনে পোড়ায় না’।
লেখক : কবি ও সাংবাদিক