

 ছবি : ড. মতিউর রহমান
ছবি : ড. মতিউর রহমান
সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে গণমানুষের অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত, শেখ আলী আহমেদ, ফয়সাল এম আহমেদ, ও মো. সাজ্জাদুল করিম রচিত গবেষণা গ্রন্থ ‘বাংলাদেশে খাসজমি-জলা : দারিদ্র্য-বৈষম্য বিমোচনের রাজনৈতিক অর্থনীতি’। গ্রন্থের মুখবন্ধের শুরুতেই গ্রন্থটির প্রধান লেখক আবুল বারকাত কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস রচিত ‘উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে’ প্রবন্ধের একটি উদ্বৃতি উল্লেখ করেছেন তা হল- ‘এশিয়ায় অবিস্মরণীয় কাল থেকে সরকারের সাধারণত শুধু তিনটি বিভাগ বর্তমান ছিল। কোষাগার বা রাজস্ব অর্থাৎ অভ্যন্তর লুণ্ঠনের বিভাগ, যুদ্ধ অর্থাৎ বহির্দেশ লুণ্ঠনের বিভাগ, এবং পরিশেষে পাবলিক ওয়ার্কসের বিভাগ। . . .পূর্ব ভারতে বৃটিশ তাদের পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে রাজস্ব ও যুদ্ধের বিভাগটি গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু পাবলিক ওয়ার্কসটা একেবারেই অবহেলা করেছে।’
ড. আবুল বারকাত গ্রন্থের মুখবন্ধে আরো উল্লেখ করেছেন, একসময় এই দেশে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না, কৃষকদের বংশানুক্রমিকভাবে জমির উপর অধিকার ছিল। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে ভূমি মালিকানার পরিবর্তন হয়েছে এবং কৃষকরা বিভিন্ন সময়ে অধিকার হারিয়েছে। বর্তমানে দেশে ৪.৫ মিলিয়ন মানুষ ভূমিহীন এবং এর কারণে তারা দারিদ্র্য ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। সরকার ভূমিহীনদের সহায়তার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলেও প্রকৃত ভূমিহীনরা নানা জটিলতার কারণে জমি বরাদ্দ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ।
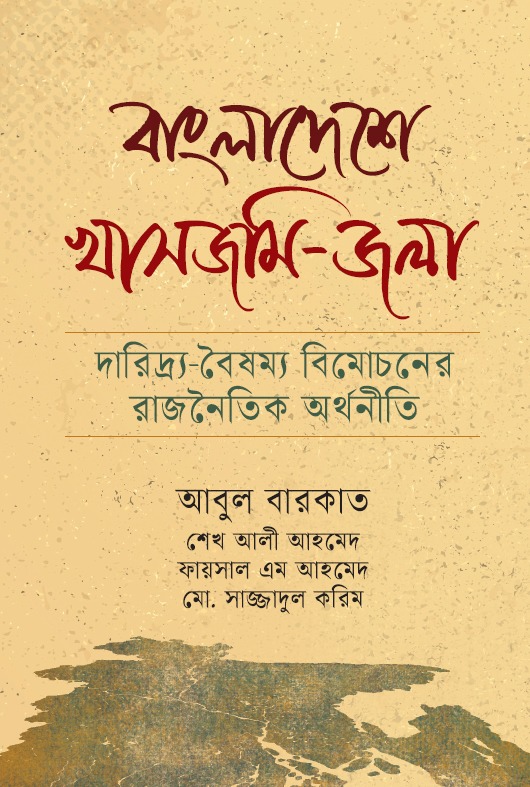 গ্রন্থটিতে মোট ১৩টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়টিতে ভূমিকা ও গবেষণাপদ্ধতি, গবেষণা এলাকা, গবেষণা ফলাফল, ভূমিহীনতার সমস্যা এবং এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে মোট ৩ কোটি ৫৫ লাখ ৩০ হাজার খানার ১১.৩৪ শতাংশের কোনো জমি নেই। আবুল বারকাত ও অন্যান্যদের (২০০১) গবেষণায় দেখা যায়, দেশে মোট খাসজমির পরিমাণ ৩.৩ মিলিয়ন একর, যার মধ্যে ০.৮ মিলিয়ন একর কৃষি খাসজমি, ০.৮ মিলিয়ন একর খাসজলা-ভূমি ও ১.৭ মিলিয়ন একর অকৃষি খাসজমি। বিভিন্ন কারণে দরিদ্র মানুষ ভূমিহীনে পরিণত হয় এবং এর ফলে তারা জীবন ও জীবিকার উপায় থেকে বঞ্চিত হয়, যা সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করে ও দারিদ্র্য বাড়ায়। সরকার ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বিতরণের উদ্যোগ নিলেও, বন্দোবস্ত প্রক্রিয়ার জটিলতা, দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতার কারণে প্রকৃত ভূমিহীনরা জমি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
গ্রন্থটিতে মোট ১৩টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়টিতে ভূমিকা ও গবেষণাপদ্ধতি, গবেষণা এলাকা, গবেষণা ফলাফল, ভূমিহীনতার সমস্যা এবং এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে মোট ৩ কোটি ৫৫ লাখ ৩০ হাজার খানার ১১.৩৪ শতাংশের কোনো জমি নেই। আবুল বারকাত ও অন্যান্যদের (২০০১) গবেষণায় দেখা যায়, দেশে মোট খাসজমির পরিমাণ ৩.৩ মিলিয়ন একর, যার মধ্যে ০.৮ মিলিয়ন একর কৃষি খাসজমি, ০.৮ মিলিয়ন একর খাসজলা-ভূমি ও ১.৭ মিলিয়ন একর অকৃষি খাসজমি। বিভিন্ন কারণে দরিদ্র মানুষ ভূমিহীনে পরিণত হয় এবং এর ফলে তারা জীবন ও জীবিকার উপায় থেকে বঞ্চিত হয়, যা সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করে ও দারিদ্র্য বাড়ায়। সরকার ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বিতরণের উদ্যোগ নিলেও, বন্দোবস্ত প্রক্রিয়ার জটিলতা, দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতার কারণে প্রকৃত ভূমিহীনরা জমি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশে খাসজমির প্রেক্ষাপট এবং ভূমি সংস্কারের ঐতিহাসিক বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ভূমির সংজ্ঞা, প্রকারভেদ (অকৃষি, কৃষি ও জলাভূমি) এবং খাসজমির ধারণা ও উৎস ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং জমিদারী প্রথার প্রভাবের পাশাপাশি ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বিতরণের বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগ ও নীতি তুলে ধরা হয়েছে। তবে, বিভিন্ন সময়ে আইনি পরিবর্তন ও উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও, প্রভাবশালী গোষ্ঠীর প্রভাব, দুর্নীতি এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে ভূমি সংস্কারের লক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হয়নি। বর্তমানে প্রচলিত খাসজমি বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালাও এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।
তৃতীয় অধ্যায়ে খাসজমিসংক্রান্ত আইন ও সংশোধনীসমূহের আলোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশে ভূমি আইনের ভিত্তি মূলত রাজস্ব আদায়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, যা কোম্পানি আমল থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঔপনিবেশিক ও পরবর্তী সময়ে বিবর্তিত হয়েছে। খাসজমির আইনি কাঠামো বিভিন্ন সময়ে প্রণীত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বেঙ্গল অ্যালুভিয়ন এন্ড ডিলুভিয়ন রেগুলেশন, বেঙ্গল টেনেন্সি অ্যাক্ট, এবং রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ও এর বিভিন্ন সংশোধনী। এসব আইনের মূল লক্ষ্য ছিল ভূমির মালিকানা নির্ধারণ, প্রজাদের অধিকার সুরক্ষা, এবং খাসজমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন করা, যদিও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জিত হয়নি, বিশেষত ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের মাঝে খাসজমি বিতরণের ক্ষেত্রে।
চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশে খাসজমি ও জলাশয়ের পরিমাণের সরকারি ভাষ্য ও গবেষণালব্ধ তথ্যের তুলনা করা হয়েছে, যেখানে ২০২৩ সালের সরকারি পরিসংখ্যানে মোট খাসজমি ও জলা ৩৫.৮ শতাংশ কম অর্থাৎ ৩৬ লক্ষ ৬০ হাজার ২৭৩ একর উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে কৃষি খাসজমি ২২ লক্ষ ৭০ হাজার ৭০৫ একর, অকৃষি খাসজমি ৮ লক্ষ ১৫ হাজার ২১২ একর এবং খাসজলা ৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ৩৫৭ একর। বিপরীতে, গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যানুসারে মোট খাসজমি ও জলাশয়ের পরিমাণ ৪৯ লক্ষ ৬৯ হাজার ১৬০ একর, যেখানে কৃষি খাসজমি ৩০ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪৫২ একর, অকৃষি খাসজমি ১১ লক্ষ ১৬ হাজার ৮৪০ একর এবং খাসজলা ৭ লক্ষ ৮৬ হাজার ৮৬৮ একর। এই গবেষণায় সরকারি তথ্যের তুলনায় ১৩ লক্ষ ৮ হাজার ৮৮৭ একর বেশি খাসজমি ও জলা চিহ্নিত করা হয়েছে, যার কারণ হিসেবে মাঠপর্যায়ে চিহ্নিতকরণে সমস্যা, মামলা, এবং বেদখলকে সম্ভাব্য কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশে খাসজমি ও জলাশয়ের বন্দোবস্তের অবস্থা নিয়ে সরকারি ভাষ্য ও গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে সরকারি হিসাব অনুযায়ী মোট খাসজমি ও জলাশয়ের ৩২.৩% বন্দোবস্ত করা হয়েছে, বিপরীতে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই হার ২৩.৮%। এর অর্থ হলো, সরকারি ভাষ্যমতে ৬৭.৭% এবং গবেষণালব্ধ তথ্যমতে ৭৬.২ শতাংশ খাসজমি ও জলা এখনও পর্যন্ত অবন্দোবস্তকৃত অবস্থায় রয়েছে। বিশেষভাবে, কৃষি খাসজমির ক্ষেত্রে সরকারি হিসাবে ৬৫.২% এবং গবেষণায় ৭৪.৩%, অকৃষি খাসজমির ক্ষেত্রে সরকারি হিসাবে ৯৪% এবং গবেষণায় ৯৫.৬%, এবং খাসজলার ক্ষেত্রে সরকারি হিসাবে ৪০% এবং গবেষণায় ৫৬.২% এখনও বন্দোবস্তের বাইরে। এই বিপুল পরিমাণ অবন্দোবস্তকৃত খাসজমি দরিদ্র ও ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য ও বৈষম্য কমানোর সুযোগ রয়েছে বলে গবেষকরা উল্লেখ করেছেন।
ষষ্ঠ অধ্যায়ে অবণ্টিত খাসজমি ও জলা ভূমিহীন, প্রান্তিক কৃষক ও মৎস্যজীবীদের মধ্যে সমবায়ের ভিত্তিতে বণ্টনের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে কৃষি খাসজমি প্রায় ৯৪ লক্ষ পরিবারকে ১৬ থেকে ২৫ ডেসিমেল, খাসজলা ১৪ লক্ষ পরিবারকে ২.৫ থেকে ৪.৯ ডেসিমেল এবং অকৃষি খাসজমির ২০% ব্যবহার করে ৩৩ লক্ষ নগর দরিদ্র পরিবারকে ৮.৫ থেকে ১১.৮ ডেসিমেল পর্যন্ত আবাসন সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে; এই বণ্টনের ফলে দেশের প্রায় ৫ কোটি ৬৪ লক্ষ দরিদ্র মানুষ উপকৃত হবে, যা দেশের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ এবং ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও দারিদ্র্য নিরসনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।
সপ্তম অধ্যায়ে বাংলাদেশে ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ এবং ১৯৮৭ সালের ভূমি সংস্কার বাস্তবায়ন কর্মসূচির (এলআরপি) মাধ্যমে প্রথম কার্যকর উদ্যোগের সূচনা হয়; এই প্রক্রিয়ায় ভূমিহীন হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্যতা, অগ্রাধিকারের তালিকা (সিকস্তি পরিবার, মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, বিধবা/তালাকপ্রাপ্ত নারী), আবেদন আহ্বান ও যাচাই-বাছাই, জমির গুণাগুণ অনুযায়ী বরাদ্দ (১ থেকে ২ একর), ৯৯ বছর মেয়াদী লিজ চুক্তি (কবুলিয়ত) সম্পাদন এবং বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মূল লক্ষ্য ভূমিহীন কৃষকদের পুনর্বাসন ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন।
অষ্টম অধ্যায়ে কৃষি খাসজমির বন্দোবস্ত প্রক্রিয়ার প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিগুলো তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে প্রচারণার অভাব, তালিকা প্রণয়নে অনিয়ম, আবেদন দাখিলে হয়রানি, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কারণে প্রকৃত ভূমিহীনদের বঞ্চিত হওয়ার চিত্র দেখা যায়; যদিও ২০০০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক পরিবার খাসজমি বরাদ্দ পেয়েছে এবং গড়ে ৫৫.৪ শতক জমি লাভ করেছে, তথাপি ৮.২ শতাংশ বরাদ্দপ্রাপ্ত পরিবার ভূমিহীন নয় এবং বরাদ্দকৃত জমির পরিমাণ প্রায়শই জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট নয়, পাশাপাশি বন্দোবস্তকৃত এলাকায় জীবিকায়ন ও দক্ষতা উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি সহায়তার অভাব পরিলক্ষিত হয়।
নবম অধ্যায়ে- জরিপ অনুযায়ী, কৃষি খাসজমি পাওয়ার যোগ্য ভূমিহীন খানার মাত্র ২৫ শতাংশ জমি পেয়েছে, যেখানে পীরগঞ্জ ও সাঘাটায় এই হার ১৬ শতাংশ এবং সুবর্ণচরে ৩০ শতাংশ; জমি পাওয়ার পরেও ১১.৬ শতাংশ দখলে রাখতে পারেনি, ১০ শতাংশ মামলায় জড়িয়েছে এবং ৯.১ শতাংশ (২.১ শতাংশ সম্পূর্ণ ও ৬.৮ শতাংশ আংশিক) বিক্রি বা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়েছে; তবে খাসজমি প্রাপ্তির সাথে নারীর বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামী পরিত্যক্ত হওয়ার কোনো সম্পর্ক পাওয়া যায়নি, কারণ ৯৭ শতাংশ প্রাপক জমি পাওয়ার সময় বিবাহিত ছিলেন।
দশম অধ্যায়ে বাংলাদেশে বন্দোবস্তকৃত খাসজমির অধিকার রক্ষা ও ভোগান্তির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে খাসজমি চিহ্নিতকরণে জটিলতা, বন্দোবস্ত প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি, নীতিমালার সীমাবদ্ধতা, ভূমিহীনদের অজ্ঞতা ও অসহায়তা, প্রভাবশালী দখলদারদের দৌরাত্ম্য, আইনি দুর্বলতা, প্রশাসনিক অদক্ষতা এবং নারীদের সীমিত অধিকারের কারণে প্রকৃত ভূমিহীনরা জমি পাওয়া ও দখলে রাখতে বহুবিধ বাধার সম্মুখীন হন; জরিপে দেখা যায়, ঘুষ ছাড়া খাসজমি পাওয়া কঠিন, দখল নিতে প্রায়শই সংঘাত হয়, মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে হয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত জমির নিয়ন্ত্রণ হারাতে হয়, যেখানে স্থানীয় প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা ভূমিহীনদের অধিকার হরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।
একাদশ অধ্যায়ে ভূমিহীনদের জীবন-জীবিকায় খাসজমির প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে ৮৫.৩ শতাংশ উত্তরদাতা খাসজমি পাওয়ার পর তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির কথা জানিয়েছেন; এর ফলে তাদের আত্মনির্ভরশীলতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে এবং সঞ্চয়, ঘরের সংখ্যা ও গবাদিপশুর সংখ্যা বেড়েছে; তবে কিছু ক্ষেত্রে জমি নিয়ে বিবাদ, অবৈধ দখল এবং আর্থিক সংকটের কারণে জমি বিক্রির ঘটনাও ঘটেছে, যা কিছু কৃষকের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করেছে।
দ্বাদশ অধ্যায়ে বাংলাদেশে খাসজমির অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিহীন সংগঠন ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর (এনজিও) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে; সুবর্ণচর ও সাঘাটার কেস স্টাডির মাধ্যমে দেখা যায়, এনজিওরা ভূমিহীনদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে, ঐক্যবদ্ধ করে এবং প্রভাবশালী ভূমিগ্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা করে; ‘নিজেরা করি’র মতো সংস্থাগুলো ভূমিহীনদের সংগঠন তৈরি, আইনি পরামর্শ প্রদান এবং খাসজমি বরাদ্দ ও দখলে রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, যা প্রান্তিক দরিদ্র কৃষকদের অধিকার আদায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচনে খাসজমির বন্দোবস্ত প্রদানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কৃষিজমির সিলিং কমানো, কার্যকর অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, আইনি সংস্কার ও ভূমিহীনদের আইনি সহায়তা প্রদান, আদালত নিষেধাজ্ঞা মোকাবিলায় ব্যবস্থা গ্রহণ, আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমি বিতরণ, খাসজমির ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি ও নিয়মিত হালনাগাদ করা, আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করা, ভূমিহীন বাছাইয়ে স্বচ্ছতা আনা, ভূমিহীনদের জন্য সমন্বিত সহায়তা প্রদান, নারীদের অধিকার সুরক্ষা, এবং এনজিও ও সামাজিক সংগঠনগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে খাসজমি বণ্টনের প্রক্রিয়াকে আরও সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও কার্যকর করে ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করা সম্ভব।
এই গ্রন্থে খাসজমি এবং জলাভূমির দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূরীকরণে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা রাখে, তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। ভূমি সংস্কারের প্রেক্ষাপট, ভূমিস্বত্বের বিবর্তন এবং ভূমিহীনদের অধিকারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। খাসজমির পরিমাণ এবং এর বন্দোবস্তের সাথে জড়িত সরকারি ভাষ্য ও গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলোর মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। ভূমিহীনদের জীবনযাত্রার ওপর খাসজমির প্রভাব এবং এই প্রক্রিয়ায় বেসরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।
এই গবেষণাগ্রন্থটির সবচেয়ে শক্তিশালী একটি দিক হলো এর তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ। বইটি ব্যাপক পরিসরের পরিসংখ্যান, ঐতিহাসিক তথ্য এবং নীতি বিশ্লেষণের সমন্বয়ে গঠিত, যা বিষয়টিকে গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করে। এছাড়াও ভূমিহীন মানুষের বাস্তব জীবনের কেস স্টাডিগুলো বইটিকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে এবং সমস্যার মানবিক দিকটি তুলে ধরেছে। ভূমিহীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সুস্পষ্ট ও কার্যকর নীতিগত এবং প্রশাসনিক সুপারিশ বইটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। লেখকরা ভূমিহীনদের অধিকারের পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছেন, যা পাঠকের মনে সহানুভূতি ও সচেতনতা সৃষ্টি করে।
প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত ও সহলেখকদের গবেষণাগ্রন্থটি খাসজমিতে ভূমিহীনদের অধিকার, জীবন-জীবিকা ও করণীয় নিয়ে আলোকপাত করেছে। বাংলাদেশে খাসজমি ও ভূমিহীনদের অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। গ্রন্থটি কৃষি খাসজমির পরিমাণ, অপব্যবহার, বন্দোবস্তের চ্যালেঞ্জ এবং ভূমিহীনদের জীবন-জীবিকায় এর প্রভাব নিয়ে গভীর অনুসন্ধান করেছে। দীর্ঘ দুই দশক পর এই বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা হওয়ায় গ্রন্থটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শূন্যতা পূরণ করবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।
এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু নীতিনির্ধারক, উন্নয়ন সহযোগী এবং সরকারি কর্মকর্তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও নীতি নির্ধারণে সহায়ক হবে। আশা করি, গ্রন্থটি সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হবে এবং ভূমি সংস্কারে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থটির দাম রাখা হয়েছে ১০০০ টাকা।
লেখক : গবেষক ও উন্নয়নকর্মী